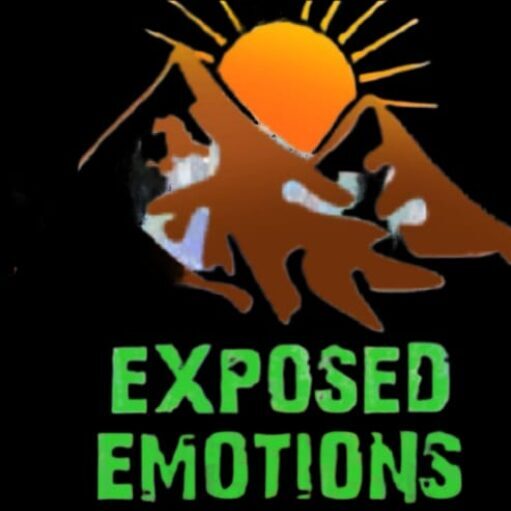সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতে ‘সুগার ড্যাডি’র সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যা প্রায় ৩,৩৮,০০০। এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে South Asian Post-এর প্রতিবেদনে। এই পরিসংখ্যান সমাজের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক চাপ, এবং সম্পর্কের জটিলতা প্রতিফলিত করে।
সুগার ড্যাডি কালচার: সংজ্ঞা ও ধারণা
‘সুগার ড্যাডি’ বলতে সাধারণত বয়সে বড়, বিত্তশালী পুরুষদের বোঝানো হয়, যারা তুলনামূলকভাবে অল্পবয়সী নারীদের আর্থিক বা উপহারের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে। এই বিনিময়মূলক সম্পর্কের মধ্যে উভয় পক্ষেরই নির্দিষ্ট প্রত্যাশা থাকে—একপক্ষ আর্থিক নিরাপত্তা পায়, অন্যপক্ষ পায় সঙ্গ বা সামাজিক মর্যাদা।
ভারতে এই কালচারের প্রসারের কারণ
- অর্থনৈতিক বৈষম্য: ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান তৈরি হয়েছে, তা অনেক তরুণ-তরুণীকে বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য করছে।
- উচ্চ শিক্ষার ব্যয়: উচ্চশিক্ষার ব্যয় এবং শিক্ষাঋণের বোঝা তরুণ প্রজন্মকে এমন সম্পর্কের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হতে পারে।
- আধুনিক জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা: বিলাসবহুল জীবনযাত্রা এবং সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেককে এই সম্পর্কের দিকে আকৃষ্ট করছে।
- ডেটিং অ্যাপ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম: অনলাইন ডেটিং অ্যাপগুলির সহজলভ্যতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর প্রচারও এই কালচারের বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে।
বিদ্যাসাগর ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন
এখনকার ‘সুগার ড্যাডি’ কালচারের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কৌলিন্য প্রথার একটি তুলনা টানা যেতে পারে। কৌলিন্য প্রথায় উচ্চবর্ণের বৃদ্ধ পুরুষরা একাধিক অল্পবয়সী কন্যার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতেন, যা পরবর্তীতে নারীদের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াত।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এই প্রথার অন্যতম কঠোর সমালোচক। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের পাশাপাশি কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতাও করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী অনুযায়ী, তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের বৈধতা প্রদানের জন্য ১৮৫৬ সালে আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
বিদ্যাসাগরের আন্দোলন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট
বিদ্যাসাগরের সময় সমাজে নারীদের অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। একাধিক বিয়ে, বাল্যবিবাহ, এবং বিধবাদের প্রতি অমানবিক আচরণ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। বিদ্যাসাগর যুক্তি ও মানবতাবাদের আলোকে এই প্রথার বিরোধিতা করেন এবং বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন নিশ্চিত করেন।
আজকের ‘সুগার ড্যাডি’ কালচার যদিও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ঘটে, তবুও এটিও নারীর আর্থিক দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর এক রূপ বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। বিদ্যাসাগরের আন্দোলন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব, যদি যথাযথ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।
উপসংহার
ভারতে ‘সুগার ড্যাডি’ কালচারের উত্থান শুধুমাত্র সম্পর্কের একটি নতুন ধারা নয়, বরং এটি সমাজের অর্থনৈতিক অসমতা, ভোগবাদী মানসিকতা, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিফলন। বিদ্যাসাগরের কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের শিক্ষা দেয় যে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব, যদি মানুষের অধিকার ও নৈতিকতার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া যায়।